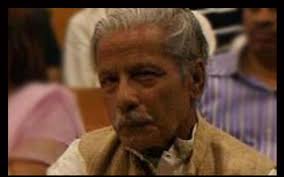(প্রবন্ধটি ইউভাল নোয়া হারারির ‘স্যাপিয়েন্সঃ মানুষ জাতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস’ বইয়ের আলোকে লেখা।)
গত তিন লক্ষ বছরে মানুষ তথা হোমো স্যাপিয়েন্স সাধারণ একটা মানুষ প্রজাতি থেকে অদ্যাবধি-পৃথিবীতে-বিচরণকারী সবচেয়ে প্রভাবশালী প্রাণীতে পরিণত হয়েছে। ভাষার বিকাশ থেকে শুরু মানুষের এ অগ্রযাত্রার ক্রমোন্নতি আজ আমাদের পরস্পরসংযুক্ত এক বিশ্বগ্রামে পৌঁছে দিয়েছে।

হ্যাঁ, মানব জাতি মানে হোমো স্যাপিয়েন্সের ইতিহাস মোটামুটি তিন লক্ষ বছরের ইতিহাস। ৪৫০ কোটি বছর বয়সী পৃথিবীর ইতিহাসে এটি আসলে খুবই অল্প সময়। পৃথিবীতে প্রথম প্রাণের উদ্ভব ঘটেছিল প্রায় ৩৮০ কোটি বছর পূর্বে। এই বিচারে, এমনকি এই গ্রহে বিবর্তিত প্রথম মানুষ প্রজাতির বিচারেও, স্যাপিয়েন্স খুব অল্প সময় ধরে এখানে বিচরণ করছে। কিন্তু এই অল্প সময়েই আমাদের অর্জন বিরাট। পৃথিবীতে আমরা যেভাবে আধিপত্য বিস্তার করেছি, অন্য কোন প্রজাতি তার কাছাকাছিও আসেনি কোন কালে।
এটা কিভাবে সম্ভব হলো? এই প্রবন্ধে আমরা মানুষের অর্জনের সেইসব চাবিকাঠির কথা বলবো। ভাষা থেকে মুদ্রা, ধর্ম, মানবতা, ইত্যাদি যা আমাদেরকে বর্তমান অবস্থায় নিয়ে এসেছে।
এক
মানুষের বৈজ্ঞানিক নাম হোমো স্যাপিয়েন্স। তবে হোমো স্যাপিয়েন্স পৃথিবীর একমাত্র কিংবা প্রথম মানুষ ছিল না। আমরা এসে মানুষের অন্য সবগুলো প্রজাতিকে প্রতিস্থাপন (replace) করে দিয়েছি। আমরা সত্যিই আলাদা। আমরা পৃথিবী নামক এই গ্রহে তো প্রভুত্ব করছিই, এমনকি মহাকাশেও পদার্পণ করেছি। হয় তো উপনিবেশও গড়বো একদিন।
কিন্তু কী করে সম্ভব হলো এতসব? এটা খুঁজে পেতে হলে আমাদেরকে মানুষ প্রজাতির বিবর্তনের কাহিনীতে ফিরে যেতে হবে।
অস্ট্রালোপিথিকাস নামক গণের গ্রেট এপ থেকে বিবর্তিত হয়ে ২৫ লক্ষ বছর আগে পূর্ব আফ্রিকায় মানুষের প্রথম উদ্ভব ঘটে। হোমো রুডোলফেনসিস ও হোমো ইরেকটাস প্রজাতির সেইসব প্রাথমিক মানুষেরা আরো ভাল পরিবেশের খোঁজে পূর্ব আফ্রিকা ত্যাগ করে। তারা যে উপযুক্ত পরিবেশ পায়, এমন নয়। ইউরোপ ও এশিয়ায় এসে নতুন পরিবেশে অভিযোজন করে তারা হোমো নিয়ানডার্থালে পরিণত (evolved) হয়।
পৃথিবীর বর্তমান মানুষ প্রজাতি হোমো স্যাপিয়েন্সের উদ্ভব ঘটে প্রায় তিন লক্ষ বছর আগে। নতুন এই প্রজাতির মধ্যে আলাদা কোন বিশেষত্ব ছিল না। এটা ঠিক যে তাদের মস্তিস্ক বড় ছিলো, তারা মাথা সোজা করে হাঁটতো, তারা যন্ত্র ব্যবহার করতো এবং খুব সামাজিক ছিলো, কিন্তু এগুলোর কোনটাই অন্য মানুষ প্রজাতিগুলো থেকে আলাদা কিছু নয়; অন্য প্রজাতিরাও ঠিক এরকমই ছিল। যেমন ধরো, নিয়ানডার্থাল প্রজাতির মানুষেরা খুব বড় প্রাণী শিকার করতে পারতো এবং বর্তমান মানুষ (স্যাপিয়েন্স) উদ্ভবের বহু বহু পূর্ব থেকেই তারা আগুনের ব্যবহার করতো। পূর্বদের থেকে বিশেষ কোন পার্থক্য না থাকার পরেও স্যাপিয়েন্স উন্নতি করলো এবং সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়লো। ওদিকে মানুষের অন্য প্রজাতিগুলো একে একে বিলুপ্ত হয়ে গেলো। কিন্তু কেন?
এ বিষয়ে দুটো তত্ত্ব (theory) রয়েছে। আন্তপ্রজনন (Interbreeding) তত্ত্ব মতে হোমো স্যাপিয়েন্স মানুষের অন্য প্রজাতি বিশেষ করে হোমো নিয়ানডার্থালের সাথে প্রজনন করতো এবং এভাবে দুটো প্রজাতি একটা আরেকটার মাঝে সম্পূর্ণরূপে লীন (merge) হয়ে গিয়েছে। এই তত্ত্বের প্রমাণ রয়েছে বর্তমান মানুষের শরীরে। বর্তমান ইউরোপিয়ানদের ডিএনএ’র ১-৪ শতাংশ নিয়ানডার্থাল ও অন্য আরো কিছু প্রজাতি থেকে আসা।
প্রতিস্থাপন (Replacement) তত্ত্ব মতে হোমো স্যাপিয়েন্স তার অধিকতর দক্ষতা ও প্রযুক্তি দিয়ে অন্য প্রজাতির মানুষদের বিলুপ্তির দিকে ঠেলে দিয়েছে। এটা হতে পারে অন্য প্রজাতির মানুষের খাদ্যের উৎস দখল করে নেয়া কিংবা সরাসরি হত্যার মাধ্যমে।
দুটো তত্ত্বের মধ্যে কোনটা সঠিক? বাস্তব নজির যতটুকু মেলে, তাতে মনে হয় দুটোই আংশিক সত্য। সম্ভবত দুটো একইসাথে ঘটেছে। হোমো স্যাপিয়েন্স তাদের হিংস্রতার মাধ্যমে অন্য প্রজাতির মানুষদের বিলুপ্তি ঘটিয়েছে, একইসাথে আন্তপ্রজননও ঘটিয়েছে।
হোমো স্যাপিয়েন্স যে এভাবে অন্য প্রজাতিদের বিলুপ্তি ঘটিয়ে দিলো, তা কিভাবে সম্ভব হলো? এর উত্তর রয়েছে মানুষের মস্তিস্কের অনন্য (unique) গঠনে।
প্রায় সত্তর হাজার বছর আগে স্যাপিয়েন্সের এক বিবর্তনীয় পরিবর্তন ঘটলো যাকে আমরা মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক বিপ্লব বলতে পারি। হঠাৎ করে মানুষের মস্তিস্ক তুলনামূলক বেশি ক্ষমতা লাভ করলো। তার চিন্তা করার ক্ষমতা জন্মালো এবং সে যোগাযোগ দক্ষতা অর্জন করলো।
এর ফলে স্যাপিয়েন্স অনেকক্ষেত্রেই তাদের প্রতিপক্ষকে মানে অন্য মানুষ প্রজাতিগুলোকে অতিক্রম করতে শুরু করলো। উদাহরণস্বরূপ, তারা আরো বড় এবং উন্নত দল গঠন করতে শুরু করলো, শিকারের জন্য আগের থেকে জটিলতর ও অধিকতর কৌশলসম্পন্ন অস্ত্র, এমনকি আগের থেকে আরো বড় বানিজ্য নেটওয়ার্ক গঠন করতে শুরু করলো।
এই সুবিধাগুলো তাদেরকে অধিকতর কঠিন পরিবেশে অন্য প্রজাতি থেকে তুলনামূলক সহজতর উপায়ে খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সম্পদাদি সংগ্রহ করতে সাহায্য করলো। যেমন, হোমো স্যাপিয়েন্সকে আমেরিকা পৌঁছাতে তীব্র শীতসম্পন্ন সাইবেরিয়া অঞ্চলকে অতিক্রম করতে হয়েছিল। সুতরাং, তারা দল গঠন করে বিশালাকার ম্যামোথ হাতি শিকার, তার চামড়া ও লোম দিয়ে তুষারে চলার জুতা ও গরম পোশাক তৈরি করতে শিখেছিল।
উন্নত শিকারের প্রযুক্তি নিয়ে মানুষ পৃথিবীর যে পথেই পা বাড়ালো, সেখানেই সে রেখে গেলো তারা অন্য প্রাণীদের বিলুপ্ত করার নিদর্শন। মাত্র ৫০,০০০ বছর আগে যখন মানুষ অস্ট্রেলিয়ায় বসবাস শুরু করলো, তখন সেখানে বাস করতো বিরাট বিরাট স্তন্যপায়ী প্রাণী। বিশ ফুট লম্বা গ্রাউন্ড স্লথ, ছোটখাট ট্রাক সাইজের আর্মাডিলো বাস করতো সেখানে। সেগুলো বিলুপ্ত হলো। মানুষের আগমনের মাত্র দুই হাজার বছরের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার বেশিরভাগ বড় প্রজাতিই পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হলো।
সোজা কথা, মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক পরিবর্তন তাকে চিন্তা ও যোগাযোগ দক্ষতা প্রদান করে যা দিয়ে সে পৃথিবীকে জয় করতে শুরু করলো।
দুই
মানুষ তথা হোমো স্যাপিয়েন্সের কোন্ বিশেষত্ব তাকে অন্য মানুষ প্রজাতিদের থেকে উন্নত করে তুললো?
৭০ হাজার বছর আগে থেকে ৩০ হাজার বছর আগের সময়টাতে সেপিয়েন্সদের নতুনভাবে চিন্তা করার এবং যোগাযোগ করার ক্ষমতার সূচনা হলো যাকে আমরা বুদ্ধিভিত্তিক বিপ্লব বলে অভিহিত করছি। আমরা এখনো সঠিকভাবে জানি না এই বিপ্লব কীভাবে সম্ভব হলো। তবে এর উত্তর হলো পরিব্যক্তি বা মিউটেশন।
(মিউটেশন কীঃ বিজ্ঞান বলে ‘জিন’ হলো জীবন্ত প্রাণের বংশগতির আণবিক একক। একটি জীবের বংশগতভাবে প্রাপ্ত বৈশিষ্ট্যগুলোর জন্য যা দায়ী, তা-ই জিন। এই জিনগুলোর বিভিন্নতার কারণে একটি জীবগোষ্ঠীর বিভিন্ন সদস্যদের মধ্যে বংশগত বেশিষ্ট্যে পার্থক্য সৃষ্টি হয়। এই ভিন্নতার কারণেই কেউ জন্মগতভাবে একটু রাগী, কেউ চুপচাপ। কেউ খেলাধুলায় চৌকস, কেউ লেখালেখিতে। জিনের অভ্যন্তরীণ গঠনের পরিবর্তনকে আমরা বলি জিনের ‘পরিব্যক্তি’ বা মিউটেশন। মিউটেশনের মাধ্যমে জীবের নির্দিষ্ট কোনো বংশধরে নতুন বৈশিষ্ট্যের উদ্ভব হতে পারে বা পুরোনো বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তনও ঘটতে পারে।)
সেপিয়েন্সদের ‘বুদ্ধিভিত্তিক বিপ্লব’ এর কারণ হিসেবে সবচেয়ে প্রচলিত মতবাদে বলা হয় মোটামুটি ৭০ হাজার বছর আগে সেপিয়েন্সদের জিনের কোন আকস্মিক পরিব্যক্তি তাদের মস্তিস্কের নিউরনের মধ্যে সংযোগের পদ্ধতি পালটে দেয়। এর ফলে তারা একে অপরের সঙ্গে আরো সার্থকভাবে যোগাযোগ করার জন্য সম্পূর্ণ নতুন এক ভাষা আয়ত্ত করতে পারে।
স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসতে পারে শুধু সেপিয়েন্সদের জিনেই কেন এই রূপান্তর হলো, নিয়ান্ডার্থাল বা মানুষের অন্যান্য প্রজাতির ক্ষেত্রে এই রূপান্তর হলো না কেন? এর উত্তরে বলা যায়, মিউটেশন বা জিনের এই রূপান্তরের ব্যাপারটা পুরোপুরি আকস্মিক। ঘটনাক্রমে এটা সেপিয়েন্সদের ক্ষেত্রে ঘটেছে, এটা নিয়ান্ডার্থাল বা মানুষের অন্য কোন প্রজাতির ক্ষেত্রেও ঘটতে পারত। আর সেরকমটা হলে আমরা মানে স্যাপিয়েন্সরা নয়, তারাই আজ পৃথিবীতে রাজত্ব করতো। যেহেতু এই রূপান্তরের কারণ সম্পর্কে আমাদের জানা নেই, তাই এর কারণের চেয়ে এর ফলে কী কী পরিবর্তন হলো সেটা জানাই আমাদের জন্য অনেক বেশি জরুরি।
যোগাযোগের জন্য প্রত্যেক প্রাণীর নিজেদের ভাষা আছে। যেমন পিঁপড়া ও মৌমাছি ভালোমতোই জানে কীভাবে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ করতে হয়, কীভাবে খাবারের খবর অন্যদের কাছে পৌঁছে দিতে হয়। যদি শুধু মুখের ভাষা বিবেচনা করি, সেই হিসেবেও সেপিয়েন্সদের এই ভাষা প্রথম ভাষা নয়। অনেক প্রাণীর, যেমন গরিলা, শিম্পাঞ্জি এবং বানরের অনেক প্রজাতির নিজস্ব মুখের ভাষা আছে। উদাহরণ হিসেবে সোনালি-সবুজ পশমওয়ালা এক জাতীয় বানরের নাম করা যায় (Green monkey), যারা একে অন্যের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য বিভিন্ন মৌখিক ধ্বনি ব্যবহার করে। জীববিজ্ঞানীরা এরকম একটি ধ্বনিসংকেত শনাক্ত করেছেন যার অর্থ, ‘সাবধান! ইগল আসছে’। একটু আলাদা আরেকটা ধ্বনিসংকেত বোঝায়, ‘সাবধান! সিংহ আসছে’। গবেষকরা যখন প্রথম ধ্বনিসংকেতটি রেকর্ড করে একদল সবুজ বানরকে শোনালেন, হুট করে বানরগুলো থেমে গেল এবং ভয়ার্ত চোখ নিয়ে ওপরের দিকে তাকাল। আবার যখন একই বানরের দলকে সিংহ আসার ধ্বনিসংকেতটি শোনানো হলো, সঙ্গে সঙ্গে বানরগুলো লাফ দিয়ে গাছে চড়ে বসল।
তিমি ও হাতিরও এরকম অনেক ধরনের ধ্বনি তৈরির ক্ষমতা আছে। আইনস্টাইন ধ্বনি ব্যবহার করে যা বলতে পারেন, একটা তোতাপাখিও শুনে শুনে সেই কথাগুলোই বলতে পারে, এমনকি সে ফোন বাজার শব্দ, দরজা ধাক্কানোর শব্দ বা দমকলের সাইরেনের শব্দও নকল করতে পারে। তার মানে বোঝা যাচ্ছে, শুধু ধ্বনি উচ্চারণ করতে পারাটাই আইনস্টাইনের বিশেষত্ব নয়। অনেক রকম ধ্বনি তৈরির ক্ষমতাকে বাদ দিলে, কী সেই বিশেষ বিষয় যার জন্য আমাদের ভাষা এতটা গুরুত্বপূর্ণ, এতটা কার্যকর? এই প্রশ্নের বেশ সহজ এবং বহুল প্রচলিত একটি উত্তর হলো, আমরা মানুষেরা কিছু সীমিতসংখ্যক ধ্বনি এবং প্রতীককে বিভিন্নভাবে জোড়া লাগিয়ে অসীমসংখ্যক বাক্য তৈরি করতে পারি, যেই বাক্যগুলো প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ বহন করে।
এইভাবে আমরা পৃথিবী সম্পর্কে অনেক রকম তথ্য জানতে পারি, জমা করতে পারি এবং অন্যদের জানাতে পারি। একটা সবুজ বানর তার সঙ্গীদের চিৎকার করে জানান দিতে পারে, ‘সাবধান! সিংহ আসছে’। কিন্তু একজন আধুনিক মানুষ তার বন্ধুকে এভাবে বলতে পারে যে, আজ সকালে নদীর ধারে একটা সিংহ একটা বাইসনকে তাড়া করছিল। সে এটাও বলতে পারে ঠিক কোন জায়গায় সে ঘটনাটা ঘটতে দেখেছে, কোন্ কোন্ রাস্তা দিয়ে জায়গাটাতে পৌছানো যায়। এই তথ্যগুলো নিয়ে তার সঙ্গী-সাথিরা আলাপ আলোচনা করতে পারে এবং সিদ্ধান্ত নিতে পারে এ অবস্থায় বাইসনটাকে শিকার করতে যাওয়াটা উচিত কাজ হবে কি না।
এর মানে হলো মানুষ ভাষা দিয়ে অন্য প্রাণীদের চেয়ে অনেক বেশি তথ্য আদান প্রদান করতে পারে।
মানুষের ভাষার বিকাশের আরেকটি তত্ত্ব হলো পরচর্চা তত্ত্ব (Gossip Theory)। এই তত্ত্ব মতে আড্ডা, খুনসুটি বা পরচর্চার জন্যই সেপিয়েন্সদের ভাষার বিকাশ ঘটেছে। যদিও পরচর্চার জন্যই ভাষার বিকাশ ঘটেছে, এই কথাটা শুনতে আপাতভাবে অনেক হাস্যকর মনে হয়, কিন্তু এ-সংক্রান্ত অনেক গবেষণাই এই তত্ত্বকে সমর্থন করে। এমনকি আজকের দুনিয়ার কথা যদি ভাবি, এখনো মানুষের সঙ্গে মানুষের বেশিরভাগ আলাপ-আলোচনার বিষয় জুড়ে থাকে অপরে কী করল, কী খেল, কোথায় কোন্ মুখরোচক বা অদ্ভুত ঘটনা ঘটলো, এসব নিয়ে; হোক সে ইমেইলে, ফোনে কিংবা সংবাদপত্রের পাতায়।
সম্ভবত ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশের কারণ হিসেবে ‘পরচর্চা তত্ত্ব’ এবং ‘নদীর-পাড়ে-একটি-সিংহ-ছিল তত্ত্ব’ এ দুটোই সঠিক। যদিও মানুষের সম্পর্কে, সিংহের সম্পর্কে বা দৃশ্যমান পৃথিবী সম্পর্কে আশপাশের মানুষকে জানানোর ক্ষমতাই মানুষের ভাষার অনন্য বৈশিষ্ট্য নয়। বরং এ ভাষার অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো এই ভাষায় মানুষ কাল্পনিক ঘটনা বা বাস্তবে যার কোনো অস্তিত্ব নেই তার গল্প করতে পারে। আমরা যতদূর জানি, সেপিয়েন্সই একমাত্র প্রাণী, যারা যেসব জিনিস কখনো চোখে দেখেনি, স্পর্শ করেনি কিংবা ঘ্রাণ নেয়নি সেসব নিয়েও অন্যদের সঙ্গে গল্প করতে পারে।
‘বুদ্ধিভিত্তিক বিপ্লব’-এর সঙ্গে সঙ্গে প্রথমবারের মতো উপকথা, পুরাণ, ঈশ্বর ও ধর্মের উদ্ভব হলো। আগে অনেক প্রাণী, এমনকি সেপিয়েন্সও বলত, ‘সাবধান! সিংহ আসছে’। বুদ্ধিভিত্তিক বিপ্লবের পর থেকেই মানুষ এরকম কথা বলার সুযোগ পেল, ‘সিংহ হলো আমাদের গোত্রের কুলদেবতা’। কাল্পনিক কথাবার্তা বলার এই ক্ষমতাই মানুষের ভাষার সবচেয়ে শক্তিশালী অংশ।
এই কথার সঙ্গে সম্ভবত আমরা সবাই একমত হব যে, একমাত্র সেপিয়েন্সই এমন সব বিষয় নিয়ে কথা বলতে পারে যেগুলোর বাস্তব কোন অস্তিত্ব নেই। একদিন সকালের নাশতা করতে বসে তারা ছয়টা বানানো গল্প বিশ্বাস করে বসতে পারে যেগুলো বাস্তবে অসম্ভব। ধরা যাক, একটা বানরকে আপনি গল্পের ছলে বললেন, আজকে যদি সে আপনাকে একটি কলা দেয়, পরকালে বানরের স্বর্গে সে ১০ হাজার কলা পাবে। বানরকে অনেক কষ্ট করে আপনি এই প্রস্তাবটা বোঝানোর পরপরই সে আপনার হাত থেকে কলাটা নিয়ে নির্লিপ্তভাবে খাওয়া শুরু করবে। সে আপনার বানানো পরকালের গল্প মোটেই বিশ্বাস করবে না। অন্যদিকে অনেক মানুষই কিন্তু ধরনের গল্প বিশ্বাস করে থাকে।
আমরা যে কেবল বাস্তবের বাইরের জিনিস কল্পনা করতে পারি তা-ই নয়, আমরা অনেকে মিলেও একই জিনিস কল্পনা করতে পারি। আমরা সবাই মিলে একসঙ্গে জগৎ কীভাবে সৃষ্টি হলো তা নিয়ে জল্পনাকল্পনা করে একেকটা সৃষ্টিতত্ত্ব দাঁড় করিয়ে তাতে বিশ্বাস করতে থাকি। আমরা অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের নিয়ে কল্পকাহিনি বানাই, আধুনিক রাষ্ট্রের জন্য কল্পনা দিয়ে বানাই ‘জাতীয়তাবাদ’। এইসব কল্পনাজাত ধারণা মানুষকে অনেক বড়ো একটা দল বা গোষ্ঠী হয়ে জীবন ধারণ করার এক অসাধারণ সুযোগ করে দেয়।
নিসন্দেহে অন্য প্রাণীরা নিজেদের মধ্যে যেভাবে যোগাযোগ করে, সে বিচারে মানুষের ভাষা অবিশ্বাস্য রকমের খটমট ও জটিল। তাই এটা স্বীকার করে নিতেই হয় যে মানুষের যোগাযোগের এই জটিল ভাষার উন্নয়নই তাকে অন্যদের ওপর প্রভুত্ব করার ক্ষমতা প্রদান করে।
মানুষ সামাজিক প্রাণী, মানে আমরা দলবদ্ধভাবে বাস করি। ভাষা তথ্যকে খুব সহজে দলে বাস করা মানুষদের ব্যক্তি থেকে ব্যক্তির কাছে পৌঁছাতে সাহায্য করে। এর মানে এই যে, গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেমন খাদ্য, বিপদজনক প্রাণী, এমনকি দলের ভেতরেই থাকা কোন বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তি, ইত্যাদি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় শিক্ষাগুলো সহজেই আদান-প্রদান করা সম্ভব হয়।
উদাহরণস্বরূপ, ভাষা দিয়ে কেউ একজন কোথাও ফলভর্তি গাছ দেখতে পেলে সেটাকে অন্যদের কাছে জায়গার বর্ণনাসহ জানিয়ে দেয়া সম্ভব হলো; কোথাও কোন বিপদজনক প্রাণীর গুহা দেখতে পেলে অন্যদেরকে সেটা সম্পর্কে সতর্ক করা সম্ভব হলো। দুটি ক্ষেত্রেই ভাষা তাকে সুস্পষ্ট সুবিধা প্রদান করলো।
কিন্তু ভাষার সবচেয়ে বড় সুবিধা সম্ভবত এগুলোর কোনটিই নয়। ভাষা মানুষকে তার দলের মধ্যে একটি সাধারণ উপলব্ধি (common understanding) তৈরি করতে সাহায্য করলো। এটিকে বলা যেতে পারে মানুষের অনন্য এক সুবিধা।
মৌমাছি বেশ বড় সংখ্যায় একত্রিত হতে পারে। কিন্তু তাদের দলবদ্ধতা এক অনমনীয় শৃঙ্খলার ভিত্তিতে গড়া। এর অর্থ যার যে কাজ তার বাইরে সে অন্য কাজ করতে পারে না; পরিবেশের পরিবর্তনে, যেমন নতুন বিপদ কিংবা সুযোগে, তারা তাদের সামাজিক বিন্যাসকে অভিযোজন করতে পারে না।
শিম্পাঞ্জির মতো কিছু প্রাণী এর চেয়ে অনেক বেশি নমনীয় সমাজশৃঙ্খলায় সংঘবদ্ধ হতে পারে। মানে তারা পরিবেশ বুঝে অভিযোজন করতে পারে। কিন্তু এসব প্রাণীর ক্ষেত্রে সমস্যা হলো তারা খুব অল্পসংখ্যক সদস্য মিলে একত্রে কিছু করতে পারে, কারণ তাদেরকে একত্রে কিছু করতে হলে পরস্পরকে খুব ভাল করে চিনতে হয়। বড় গ্রুপের জন্য যা মোটেই সুবিধাজনক নয়।
পৃথিবীতে মানুষই একমাত্র প্রাণী যারা বড় সংখ্যায় এবং নমনীয় শৃঙ্খলায় সংঘবদ্ধ হতে পারে। এর কারণ আমরা ভাষার মাধ্যমে পার্থিব জগত বিষয়ক তথ্য একে অন্যের সাথে আদান প্রদান করতে পারি; আমরা ঈশ্বর, ইতিহাস, জাতীয়তাবাদ, মানবাধিকার, ইত্যাদি বিমূর্ত ধারণাগুলো (abstract ideas) সম্পর্কে আলোচনা করতে পারি। এই বিমূর্ত ধারণাগুলো আসলে মানব মস্তিস্কপ্রসূত কিছু সাধারণ মিথ, যাতে পৃথিবীর প্রায় সব মানুষই বিশ্বাস করে। এগুলোই আসলে মানব সংস্কৃতির ভিত্তি, এবং এগুলোই আমাদেরকে ব্যক্তিগতভাগে পুরোপুরি অপরিচিত লোকের সাথেও একত্রিত হয়ে বিরাট দলে সংঘবদ্ধ হতে এবং একটি সাধারণ লক্ষ্যে কাজ করতে সাহায্য করে।
মানব প্রজাতির প্রাথমিক লগ্নে মানুষ ছোট ছোট দলে বাস করতো। দলগুলো সাধারণত ১৫০ জনের বেশি হতো না। কিন্তু ভাষার উন্নতির ফলে এবং কিছু সাধারণ মিথে বিশ্বাস করার ফলে আমরা আমাদের সমাজের আয়তন ক্রমশ বাড়াতে পেরেছিঃ গ্রাম থেকে শহর, শহর থেকে জাতিরাষ্ট্র, এবং জাতিরাষ্ট্র থেকে বর্তমান সময়ের বৈশ্বিক সমাজ।
তিন
মানুষের ইতিহাসের বেশিরভাগ সময়ই মানুষ যাযাবর জীবন যাপন করতো। আমাদের পূর্ব পুরুষগণ তাদের জীবন অতিবাহিত করতো শিকার করে ও অন্যান্য খাদ্যশস্য সংগ্রহ করে। কোন এক জায়গায় স্থিত হয়ে বসবাস না করে তারা ক্রমাগত জায়গা পরিবর্তন করেছে। তাদের স্থানান্তরের প্রধান কারণই ছিল খাদ্য। এক স্থানে খাদ্য সংকট দেখা দিলে অন্য যেখানে খাদ্যের প্রাচুর্যতা রয়েছে সেখানে চলে যেতো তারা।
প্রায় ১২০০০ বছর আগে এই অবস্থার পরিবর্তন হতে শুরু করলো। মানুষ খাদ্যের জন্য কেবল শিকার ও সংগ্রহের ওপর নির্ভর না করে খাদ্যশস্য চাষ ও পশুপালন করতে শুরু করলো। বর্তমান থেকে প্রায় ১০০০০ বছর আগে পৃথিবীর প্রায় সকল অঞ্চলের মানুষই শিকার ও সংগ্রহ পরিত্যাগ করে কৃষিতে স্থিত হয়ে গেলো। সত্যিকারার্থেই এটা ছিল একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন। আমরা তাই এটাকে মানুষের কৃষি বিপ্লব বলে অবহিত করে থাকি। এ সময়ে যে বড় পরিবর্তনটা ঘটলো তা হলো, সংখ্যায় মানুষ অনেক বেড়ে গেলো।
মানুষের শিকারী-সংগ্রাহক অবস্থা পরিত্যাগ করে কৃষিকে অগ্রাধিকার দেয়া একটু বিস্ময়করই বটে। শ্রমের কথা বিবেচনা করলে কৃষি মানুষের জন্য অনেক বেশি সময়ক্ষেপক। যেখানে শিকার ও সংগ্রহের পিছনের একজন মানুষ দিনে চার ঘণ্টা ব্যয় করলেই হতো, সেখানে একজন কৃষকের সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ করতে হতো।
বর্তমান যুগের একটা উদাহরণ দিয়েই বিষয়টা পরিস্কার করা যাক। যেখানে আজকের প্রাচুর্যপূর্ণ সমাজেও মানুষজন সপ্তাহে গড়পড়তা প্রায় ৪০ থেকে ৪৫ ঘণ্টা কাজ করে, উন্নয়নশীল দেশে প্রায় ৬০ এমনকি ৮০ ঘণ্টা কাজ করে, সেখানে কালাহারি মরুভূমির মতো প্রতিকূল পরিবেশেও আজকের দিনের শিকারি-সংগ্রাহকরা সপ্তাহে মাত্র ৩৫ কি ২৫ ঘণ্টা কাজ করে। তারা প্রতি তিন দিনে এক দিন শিকার করে। অন্যান্য খাবার সংগ্রহের কাজটা করতে তিন থেকে ছয় ঘণ্টা নেয় বড়োজোর। সাধারণত একটা গোষ্ঠীর জন্য এটাই যথেষ্ট হয়। এমনও হতে পারে যে, এখনকার কালাহারি মরুভূমির চেয়েও বেশি উর্বর জায়গায় প্রাচীন শিকারি মানুষেরা খাবার বা বিভিন্ন কাঁচামাল জোগাড় করার জন্য অনেক কম সময় ব্যয় করত। তার ওপর, শিকারি-সংগ্রাহকদের ক্সদনন্দিন জীবনযাপনের জন্য অনেক কম কাজ করতে হতো। তাদের থালা-বাটি ধোয়া, ঘর পরিস্কার করা, বাচ্চার কাঁথা বদলানো বা বিল পরিশোধ করার মতো বিরক্তিকর কাজগুলো করতে হতো না।
কৃষিভিত্তিক সমাজে অতিরিক্ত সময় কাজ করার অন্যতম আরেকটি কারণ ছিল ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা। মানুষ জানতো না পরবর্তী বছর ঠিকমতো বৃষ্টি হবে কিনা বা খাদ্যশস্যে পোকা লাগবে কিনা। ফলে তাকে অতিরিক্ত উৎপাদন করে পরবর্তী বছরের জন্য খাদ্য মজুদ করতে হতো।
একইসাথে পুষ্টিমানেও কৃষি উৎপাদিত খাদ্য ছিল নিকৃষ্টতর। প্রথমদিকের কৃষকদের কাছে উৎপাদিত খাদ্যশস্যের বৈচিত্র ছিল খুবই কম। প্রধানত গমজাতীয় খাদ্যশস্য, যা তারা ফলাতো, তা হজমে ছিল কঠিন। অন্যদিকে শিকারী-সংগ্রাহক অবস্থার খাদ্য মাংস, বাদাম, ফল, মাছ, ইত্যাদির থেকে পুষ্টি ও ভিটামিনে ছিল অনুন্নত।
এ ছাড়াও কোনো একটা নির্দিষ্ট খাবারের ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল না হওয়ার ফলে কোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে শিকারী-সংগ্রাহকদের অনেক কম ভুগতে হতো। অন্যদিকে কৃষিভিত্তিক সমাজগুলো প্রায়ই দুর্ভিক্ষে ধ্বংস হয়ে যেত। খরা, দাবদাহ বা ভূমিকম্পের মতো বড়ো বড়ো প্রাকৃতিক দুর্যোগ তাদের ধান কিংবা আলুর খেত লণ্ডভণ্ড করে দিত। অবশ্য শিকারি-সংগ্রাহকদের যে এইসব প্রাকৃতিক দুর্যোগে কোনো সমস্যা হতো না, এরকম ভাববার কোনো কারণ নেই। তাদেরও সমস্যা হতো, তারাও অনেক সময় না খেয়ে থাকত কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, তাদের জন্য এই ধরনের দুর্যোগ থেকে উত্তরণটা অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল। তাদের কোন একটা নিয়মিত খাবারের উৎস যদি ধ্বংসও হয়ে যেত, তারা তখন অন্য কোনো কিছু দিয়ে কাজ চালিয়ে নিত অথবা অন্য কোথাও চলে যেত। আরো মজার ব্যাপার হলো, প্রাচীন শিকারি-সংগ্রাহকরা সংক্রামক রোগে অনেক কম আক্রান্ত হতো। কৃষি কিংবা শিল্পভিত্তিক সমাজে যে সমস্ত রোগ মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়েছিল (যেমন গুটিবসন্ত, হাম, যক্ষা) সেগুলোর বেশিরভাগেরই উৎপত্তি আসলে গৃহপালিত পশুপাখি থেকে। এইসব রোগজীবাণু পরবর্তী সময়ে মানুষের শরীরে স্থানান্তরিত হয় মূলত কৃষিবিপ্লবের পরে, আগে নয়। যেসব প্রাচীন শিকারি-সংগ্রাহকরা শুধু কুকুরকে পোষ মানিয়েছিল তারাও এইসব পরিণতি থেকে মুক্ত ছিল। তা ছাড়া কৃষি বা শিল্পভিত্তিক সমাজের বেশিরভাগ মানুষই বসবাস করত খুব অস্বাস্থ্যকর, ঘনবসতিপূর্ণ চিরস্থায়ী বসতিতে, যেগুলো ছিল রোগজীবাণুর আদর্শ বাসস্থান। অন্যদিকে শিকারি-সংগ্রাহকরা ছোটো ছোটো গোষ্ঠীতে আলাদা আলাদাভাবে ঘুরে ঘুরে বেড়াত। তার ফলে কোনো রোগই মহামারির আকার ধারণ করতে পারত না।
তাহলে কেন এই পরিবর্তন?
এর প্রধানত দুটো কারণ ছিল। প্রথমত, শিকারী-সংগ্রাহক অবস্থা থেকে কৃষিতে স্থিত হওয়া ছিল খুবই ধীর একটি প্রক্রিয়া। প্রথমদিকে তারা দুটোতেই অভ্যস্ত ছিল, কিন্তু ক্রমে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে আশেপাশের এলাকাগুলো অতিরিক্ত শিকার ও সংগ্রহে খাদ্যশূন্য হয়ে পড়েলে মানুষ ক্রমশ কৃষির ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। একটা পর্যায়ে যখন তারা বুঝতে পারে যে তাদের এভাবে কৃষিতে স্থিত হওয়া ভুল হয়ে গিয়েছে, তখন আর পেছনে ফেরার উপায় ছিল না।
দ্বিতীয়ত, যতোই ত্রুটি থাকুক কৃষিব্যবস্থায় মানুষ সবচেয়ে বড় যে সুবিধাটা পেলো তা হলো তারা খুব অল্প জায়গায় অনেক বেশি খাদ্যশস্য উৎপাদন করতে পারলো। আর কোন গোষ্ঠীতে খাদ্যের প্রাচুর্যতা মানে ঐ গোষ্ঠীর অতিরিক্ত জনসংখ্যার ভরণ-পোষণ দেয়ার সক্ষমতা। ফলে জনসংখ্যা গেলো বেড়ে। এবার অতিরিক্ত জনসংখ্যা, গৃহস্থালী সাজ-সরঞ্জাম এবং সাথে অনেকসংখ্যক পোষ্য প্রাণী নিয়ে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গমন হয়ে পড়লো অসম্ভব।
চার
জনসংখ্যা বৃদ্ধি মানুষের জন্য এক বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো। এত মানুষের সাথে সম্পর্ক স্থাপন এবং তা রক্ষা ও বিনিময় চালানোর মতো না ছিল তাদের অভিজ্ঞতা, না ছিল কোন মাধ্যম। এই প্রয়োজন থেকেই উদ্ভব হলো অর্থ এবং লিপির।
কৃষি বিপ্লবের পূর্বে মানুষের জীবন ছিল তুলনামূলকভাবে সরল। বেশিরভাগ শিকারী-সংগ্রাহকরাই ছোট ছোট গোত্রে বাস করতো, আর গোত্রভিত্তিক সমাজে যেহেতু ব্যক্তিসম্পদের বালাই ছিল না, তাই লেনদেনের কোন ব্যাপার ছিল না। নিজেদের প্রয়োজনীয় সব জিনিস তারা শিকার করে বা কুড়িয়ে পেত, অথবা বানিয়ে নিত নিজেরাই। খাবার, ওষুধ, জামা, জুতা, সবকিছুই। গোষ্ঠীর একেকজন মানুষ একেকটা কাজে পারদর্শী হতো বটে, তবে তারা একে অপরকে সাহায্য করত সব সময়।
কৃষি বিপ্লবের ফলে গোত্রভিত্তিক সমাজ ভেঙে ক্রমে পরিবারভিত্তিক সমাজ তথা গ্রাম গঠিত হতে থাকে। তবে সামাজিক বা অর্থনৈতিক নিয়মাদির খুব একটা পরিবর্তন তখনও হয়নি। তোমার পরিবারে মাংসের সংকট হলো, তুমি তোমার প্রতিবেশী, যার কাছে অতিরিক্ত আছে, তার কাছে চাইলেই হলো। যদি সে নিশ্চিন্ত হতে পারে যে তার দুঃসময়ে তুমি তাকে সাহায্য করবে, তোমাকে মাংস দিয়ে দিলো। কিন্তু কৃষির উন্নয়নের ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটা ভেঙে গেলো। এর পরিবর্তে সূচনা হল বিনিময় ব্যবস্থার।
কৃষি ব্যবস্থা চালু হওয়ায় মানুষ পর্যাপ্ত খাদ্য উৎপাদনে সক্ষম হলো। কিন্তু কৃষিতে শিকারের চেয়ে অধিক যন্ত্রপাতি প্রয়োজন হওয়ায় যারা সেসব যন্ত্রাদি অন্যদের চেয়ে দক্ষতার সাথে প্রস্তুত করতে পারতো তারা নতুন ধরণের ব্যবসা শুরু করলো। তারা কৃষকের কাছে খাদ্যের বিনিময়ে ছুড়ি, কোদাল, লাঙল, বেলচার মতো যন্ত্রাদি বিক্রি করতে শুরু করলো। তাদের পথ ধরলো কাপড় বুনন, চিকিৎসাসহ অন্য পেশাতে দক্ষ লোকেরা।
জনসংখ্যার আধিক্য নিয়ে এ সময়ে কোথাও কোথাও প্রতিষ্ঠিত হলো নগর। শীঘ্রই দেখা গেলো বিনিময় অর্থনীতি আর তাদের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হচ্ছে না। ব্যবসায়ের পরিধি যত বাড়তে লাগলো, ততোই এটা জানা বা মনে রাখা খুব কঠিন হয়ে দাঁড়ালো কার পণ্য তোমার প্রয়োজন আর তোমার পণ্য কার প্রয়োজন।
একটা উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি পরিস্কার করা যাক। ধরো, এক কামারের কাছে কিছু ছুড়ি আছে, যার বিনিময়ে সে কিছু শুকরের মাংস চায়। কিন্তু দেখা গেলো যে চাষীর কাছে শুকর আছে, তার কাছে ছুড়িও আছে। আবার যে চাষীর ছুড়ি প্রয়োজন, তার কাছে এই মুহূর্তে বিনিময়যোগ্য শুকর নেই। চাষী কামারকে কথা দিলো যে সে তার কাছ থেকে এখন ছুড়ি নিবে, কিন্তু যখন তার বিনিময়যোগ্য শুকর হবে, তখন সে কামারকে একটা শুকর দিবে। কিন্তু চাষী যে তার কথা রাখবে, এ ব্যাপারে কামার যদি নিশ্চিত হতে না পারে, তাহলে কী হবে?
গ্রামে তবুও এটা কোনরকমে চালিয়ে রাখা যাচ্ছিল, কিন্তু নগরগুলোতে এটা হয়ে পড়েছিল একেবারেই অসম্ভব। অনেকগুলো অচেনা মানুষ নিয়ে গড়ে ওঠা একটা সমাজে এরকম বিনিময় প্রথা চালু রাখার অসুবিধা অনেক। নিজের পরিবারের সদস্য বা প্রতিবেশীদের সাহায্য করা সহজ, কিন্তু বহিরাগত মানুষকে সাহায্য করে বিনিময়ে কিছু পাওয়ার নিশ্চয়তা কতখানি? প্রায় তিন হাজার খ্রিস্ট পূর্বাব্দে ঠিক এ ধরণের সমস্যা থেকেই লিখন পদ্ধতি ও মুদ্রার উদ্ভব ঘটায় মানুষ।
মানুষের প্রথম মুদ্রা কিন্তু কোন ধাতব মুদ্রা ছিল না। একেক সভ্যতায় একেক রকম মুদ্রার প্রচলন দেখা যায়। সবচেয়ে বেশি দেখা যায় কড়ির ব্যবহার। আসলে প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার কড়ি থেকে আধুনিক সভ্যতার টাকা বা ডলার, যে রূপেই থাকুক, মুদ্রা বা টাকা মূল্যবান, কারণ এর মূল্য আছে আমাদের সম্মিলিত কল্পনায়। এই মূল্য কড়ির রাসায়নিক গুণাগুণ বা কাগজের রং বা আকার-আকৃতির জন্য নয়। অন্যভাবে বলতে গেলে টাকা আসলে কোনো বস্তু নয়, একটা মানসিক ধারণা মাত্র। আমরা যখন কিছু বিক্রি করে টাকা নিই, তখন টাকা বাস্তব বস্তুকে রূপান্তরিত করে একটা কাল্পনিক বস্তুতে।
টাকা কাজ করে মানুষের সম্মিলিত কল্পনার ওপর বিশ্বাসের জন্যে। পৃথিবীতে যত রকম মুদ্রাব্যবস্থা চালু আছে, তাদের প্রত্যেকটার মূল ভিত্তি হলো এই বিশ্বাস। একজন কৃষক যখন কিছু কড়ির বিনিময়ে তার সব সম্পত্তি বেচে দিয়ে দূরদেশে পাড়ি জমায়, সে তখন বিশ্বাস করে যে সে যেখানে যাচ্ছে সেখানকার মানুষও এই কড়ির বিনিময়ে তাকে খাবার ও আশ্রয় দিবে। আসলে টাকা হলো সারা পৃথিবীর মানুষের সর্বজনীন ও সর্ববৃহৎ সমন্বিত বিশ্বাসের আধার। আমি কেন কড়ি, স্বর্ণমুদ্রা বা কাগজের নোটে বিশ্বাস করব? আমি বিশ্বাস করব কারণ আমার আশপাশের সব মানুষ এতে বিশ্বাস করে। আবার আমার আশপাশের মানুষ বিশ্বাস করে, কারণ আমি এতে বিশ্বাস করি। আমরা সবাই বিশ্বাস করি, কারণ দেশের রাজাও এতে বিশ্বাস করেন; তিনি খাজনা আদায় করেন এর মাধ্যমেই।
শুরুতে যখন ‘টাকা’ জিনিসটার প্রচলন হয়, তখন এই বিশ্বাসের ব্যাপারটা ছিল না। তাই তখন মুদ্রা হিসেবে ব্যবহৃত হতো এমন কিছু, যার একটা সত্যিকারের মূল্য আছে। মানুষের জানামতে, প্রথম অর্থ ছিল সুমেরীয় এলাকায় ব্যবহৃত বার্লি-টাকা।
টাকার ইতিহাসে সবচেয়ে বড়ো বিপ্লবটি ঘটে যখন মানুষ আপাতমূল্যহীন, সঞ্চয় ও বহনযোগ্য কোনো বস্তুকে মুদ্রা হিসেবে গ্রহণ করে। সেটা ঘটেছিল খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দের মাঝামাঝি সময়ে, মেসোপটেমিয়াতে। রূপাকে মুদ্রা হিসেবে গ্রহণ করে সেখানকার মানুষ। এর একক ছিল শেকেল।
মজার ব্যাপার হলো টাকা হিসেবে বার্লির প্রচলন হয়েছিল ৩০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের দিকে, ঠিক যখন মানুষ সেই একই জায়গায় লিখনপদ্ধতি আবিস্কার করে। এই দুটো ঘটনা সমসাময়িক হওয়ার কারণ হলো, মানুষ লিখতে শুরু করে মূলত তাদের প্রশাসনিক কাজকর্মের সুবিধার্থে। আর প্রশাসনিক তৎপরতা বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডও বেড়ে যায়। সেই বর্ধিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার চাহিদা পূরণ করতেই টাকার উদ্ভব।
লিখন পদ্ধতি চালু হলে অর্থনীতিতে এর বিশাল প্রভাব পড়ে। এর ফলে মানুষের পক্ষে অপেক্ষাকৃত জটিল ব্যবসায়িক তথ্য সংরক্ষনে সুবিধে হয়। প্রথম দিকে তারা মাটির স্লেটে দাগ এঁকে কিছু চিহ্নের মাধ্যমে হিসাব রাখতে শুরু করে। ওপরে যে শুকর চাষী ও কামারের উদাহরণ দেয়া হয়েছিল, মুদ্রা ও লিখন পদ্ধতি আবিস্কারের ফলে তারা তাদের সমস্যার সমাধান খুঁজে পেলো সহজেই। বর্তমানে চাষীটির বিনিময়যোগ্য শুকর নেই বটে কিন্তু টাকা আছে। সে টাকা দিয়ে ছুড়ি কিনতে পারলো, আর কামার সেই টাকা দিয়ে অন্য শুকর চাষীর কাছ থেকে শুকর কিনতে পারলো। অথবা, কামার রেকর্ড রাখতে পারলো অমুক শুকর চাষী তার কাছ থেকে ছুড়ি নিয়েছে এবং বিনিময়ে সে কামারকে পরে একটি শুকর দিবে। এই রেকর্ড দিয়ে সে পরে তার কাছ থেকে প্রতিশ্রুত শুকরটি আদায় করে নিতে পারবে।
পাঁচ
আমরা যেমনটা দেখেছি লিপি ও অর্থের প্রচলন অর্থনৈতিক লেনদেনকে সহজ করেছে ও প্রতারণাকে করেছে কঠিন, তবে এমনটা মনে করার কারণ নেই যে হঠাৎ করে অর্থনীতি খুব সাবলীলভাবে চলতে শুরু করেছিল। বস্তুত, এর ফলে সমাজ ও অর্থনীতি দ্রুত বেড়ে সবকিছু আরো জটিল থেকে জটিলতর হয়ে যায়। ফলে সমাজ ও অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করা হয়ে উঠলো কঠিনতর।
সমাজ ও অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে এবার প্রয়োজন পড়লো আইনের। আর মানুষ যাতে আইন মানতে বাধ্য হয়, তাই তা প্রয়োগের জন্য তৈরি করতে হলো আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষের। আর এভাবেই প্রথম শ্রেণীভিত্তিক (hierarchical) সমাজের জন্ম হয়, যার সবচেয়ে উচুতে অবস্থান করে একজন রাজা বা সম্রাট।
যদিও বর্তমানে আমরা রাজা বা সম্রাটকে স্বেচ্ছাচারী ও নিষ্ঠুর শাসক হিসেবে দেখে থাকি, বাস্তবে রাজতন্ত্র এবং সাম্রাজ্য ব্যবস্থা রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্থিতাবস্থা আনতে সাহায্য করেছে। এর ফলে একটি কার্যকর আমলাতন্ত্র চালু হয়েছিল যা পুরো রাজ্যজুড়ে আইন ও প্রথার সমকরণ করেছে।
উদাহরণ হিসেবে হাম্মুরাবি কোডের কথা বিবেচনা করা যাক। ১৭৭৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ব্যবিলনীয় রাজা হাম্মুরাবি যে আইনমালা লিপিবব্ধ ও প্রয়োগ করেন, সেটি হাম্মুরাবি কোড নামে পরিচিত। এই আইনের প্রয়োগ ছিল পুরো ব্যবিলনীয় রাজ্যে, যার মাধ্যমে শুল্ক নির্ধারণ করা হতো; চুরি/ডাকাতি/হত্যাসহ অন্যান্য অপরাধের বিচার করা হতো। ফলে পুরো সাম্রাজ্যের মানুষ জানতো কোনটা করা যাবে আর কোনটা করা যাবে না। রাজ্যের মধ্যে যেখানেই ভ্রমণ করুক বা ব্যবসায়ের জন্য যাক না কেন, মানুষকে আলাদা আইন নিয়ে চিন্তিত হতে হতো না।
আইনের প্রয়োগের জন্য রাজা বা সম্রাটের কর্তৃত্বের প্রতি জনগণের গ্রহণযোগ্যতা দরকার ছিল। প্রায় সকল রাজা বা সম্রাটই এখানে ধর্মের প্রয়োগ ঘটান। যদি জনগণ এটা বিশ্বাস করানো যেতো যে তাদের শাসককে সর্বোচ্চ আসনে বসিয়েছেন ঈশ্বর, তাহলে আর ঐ রাজার আইন প্রয়োগে কোন সমস্যা হতো না। উদাহরণস্বরূপ, রাজা হাম্মুরাবি তার শাসন ও আইনকে বৈধতা দেয়ার জন্য ঘোষণা করেছিলেন যে মেসোপটেমিয়ার জনগণকে শাসন করার জন্য তাঁকে রাজা হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন স্বয়ং ঈশ্বর।
সাম্রাজ্য বিস্তারের সাথে চলেছে শাসকের ধর্ম বিস্তার। একদিকে এটি যেমন শাসককে শক্তি যুগিয়েছে, পাশাপাশি ধর্ম নিজেও ক্রমশ শক্তি অর্জন করেছে। কখনো শক্তি প্রয়োগে, কখনো বা ক্রমাগত আত্তীকরণের মাধ্যমে সাম্রাজ্যগুলো বিবিধ জাতিগত ও ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলোকে একটি বড় মেগাসংস্কৃতিতে রূপান্তরিত করেছে। এক কথায় বলতে গেলে, সাম্রাজ্য ও ধর্মের সমন্বয় বহুধাবিভক্ত মানবজাতিকে একটি বৈশ্বিক ঐক্যবন্ধনের দিকে ঠেলে দিয়েছে।
ছয়
পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্বের প্রায় পুরোটা ধরেই মানুষকে একটি নৈরাশ্যবাদী প্রাণী বলা চলে। ইতিহাসজুড়ে দেখা যায় বেশিরভাগ মানুষই তাদের নিজেদের সামর্থ্যে বিশ্বাস না করে একজন সর্বশক্তিমান ঈশ্বরে বিশ্বাস করেছে। যেহেতু প্রতিটি মানুষের ওপরে ঈশ্বরের সার্বিক নিয়ন্ত্রণ ছিল, মরণশীল মানুষের কাছে জ্ঞান আহরণ ও বৈজ্ঞানিক উন্নতির প্রচেষ্টাকে অর্থহীন মনে হয়েছে। তার চেয়ে বসে থেকে নিয়তির জন্য অপেক্ষা করাই ভাল মনে করেছে তারা।
অবশেষে ষোড়শ শতাব্দীতে এসে মানুষের নৈরাশ্যবাদীতার পরিবর্তন ঘটতে শুরু করে। এ সময়ে এবং এর পরবর্তী শতাব্দীতে পুরো ইউরোপ জুড়ে একটি বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের জোয়ার আসে। ঈশ্বরের অপেক্ষায় বসে না থেকে মানুষ চিন্তা করতে শুরু করে কিভাবে বিজ্ঞানের প্রয়োগে তারা নিজেরাই সমাজের উন্নয়ন ঘটাতে পারে। বৈজ্ঞানিক মূলনীতি যথা অনুসন্ধান, পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের প্রয়োগের মাধ্যমে মানুষ চিকিৎসা, জোতির্বিদ্যা এবং পদার্থবিদ্যায় অভূতপূর্ব উন্নতি করে যা সমাজগুলোকে অধিকতর বাসযোগ্য করে তোলে।
উদাহরণস্বরূপ শিশু মৃত্যুর হার উল্লেখ করা যেতে পারে। যখন থেকে ওষুধ ও গণস্বাস্থ্যে বিজ্ঞানলব্ধ জ্ঞানের ব্যবহার শুরু হয় তখন থেকে শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস পেতে শুরু করে। পূর্বে ধনী পরিবারেও দুই/তিনটি শিশুর অকাল মৃত্যু খুব সাধারণ ছিল। বর্তমানে তা কমে কমে হাজার জনসংখ্যায় মাত্র একজনে নেমে আসে।
সুস্বাস্থ্যের সাথে যে অর্থনৈতিক সুস্বাস্থ্যও সম্পর্কিত- ইউরোপিয়ান সরকারগুলো এটি খুব তাড়াতাড়ি বুঝে ফেলে। কেবল স্বাস্থ্য নয়, নতুন নতুন আইডিয়া ও নতুন সম্পদের খোঁজে রাজা ও সম্রাটগণ দু’হাত ভরে বিনিয়োগ করতে শুরু করেব। স্পেনের রাজা কলম্বাসের আটলান্টিক পাড়ি দেয়ার অর্থ যোগালেন। বিনিময়ে তিনি পেলেন সোনা রূপায় সমৃদ্ধ বিরাট আমেরিকান সাম্রাজ্য।
একইভাবে ব্রিটিশ সরকার জেমস কুককে আর্থিক সহায়তা দিয়ে দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চল অনুসন্ধানে পাঠায়, যার ফলস্বরূপ আবিস্কৃত হলো অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড। উভয় ক্ষেত্রেই লাভবান হলো ইউরোপিয়ান অর্থনীতি। এটি সম্ভব হয়েছিল কেবল ইউরোপিয়ান সরকারগুলোর বিজ্ঞান ও অনুসন্ধানে ব্যয়ের ফলে, যদিও এর জন্য বিরাট মূল্য দিতে হয়েছিল সেখানকার আদিবাসী জনগণকে।
স্পেন ও ব্রিটেনের সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে ইউরোপিয়ান রাষ্ট্রগুলো ছড়িয়ে পড়ে বিশ্বের আনাচে কানাচে এবং এশিয়া, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া ও আমেরিকায় তাদের উপনিবেশ গড়ে তোলে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে কেবল বিট্রিশ সাম্রাজ্যই পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক ভূমিতে তাদের বিস্তার কায়েম করে।
ইউরোপিয়ান রাষ্ট্রগুলো যেখানেই তাদের সাম্রাজ্য বিস্তার করেছে, সেখানেই তারা নতুন ধারণা, মতবাদ ও ধর্ম প্রচার করতে শুরু করে। স্থানীয় প্রথা, সংস্কৃতি, আইনকে প্রতিস্থাপন করে ইউরোপিয়ান সাংস্কৃতিক আদর্শ দিয়ে। সবচেয়ে বড় যে ইউরোপিয়ান আদর্শটি পৃথিবীজুড়ে বিস্তার লাভ করে সেটি পুঁজিবাদ।
ইউরোপিয়ান সাম্রাজ্যগুলোকে দেখেই আমরা অর্থের গুরুত্ব ও শক্তিতে বিশ্বাস করতে শিখেছি। বলা যায়, পুঁজিবাদের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা বর্তমান বৈশ্বিক সমাজ আসলে ইউরোপিয়ান সাম্রাজ্যবাদেরই উত্তরাধিকার। বর্তমানে ইউরোপিয়ান সাম্রাজ্যগুলো তাদের উপনিবেশ গুটিয়ে নিয়েছে বটে, কিন্তু আমরা এখনও তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে বহন করে চলছি।
আজ ব্রাজিল কিংবা ভুটান, কানাডা কিংবা কলম্বিয়া, যে যেখানেই বাস করুক না কেন, প্রায় সব মানুষই অর্থ ও বস্তুকেন্দ্রিক জীবন যাপন করছে। আমরা সবাই-ই চাই আমাদের আয় বৃদ্ধি করতে, এবং পোশাক-আশাক ও সাজ-সজ্জা দিয়ে সম্পদের প্রদর্শন করতে।
বিজ্ঞান ও পুঁজিবাদের সমন্বয় পৃথিবী থেকে অনেক পুরোনো আদর্শকে ক্রমশ বিলুপ্তির দিকে নিয়ে গেছে। এর অন্যতম উদাহরণ ধর্ম। আধুনিক বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে ধর্মীয় নীতি ও তত্ত্বগুলোর বেশিরভাগই ভুলে ভরা। আজ আমাদের অধিকাংশই বিশ্বাস করি না যে ঈশ্বর নামক কোন শক্তি সাত দিনে পৃথিবী সৃষ্টি করেছিল। জীব জগতের ক্ষেত্রে আমরা প্রাকৃতিক নির্বাচনভিত্তিক ডারউনের বিবর্তন তত্ত্বে বিশ্বাস করি।
ধর্মীয় তত্ত্বগুলো যখন প্রশ্নের মুখে পড়ছে, তখন এগিয়ে আসছে পুঁজিবাদী ভাবাদর্শ। মৃত্যুপরবর্তী জীবনে সুখের অপেক্ষায় না থেকে মানুষ আজ ইহজীবনের সুখবৃদ্ধিতে মনযোগ দিয়েছে। আরেকটু সুখের আশায় আমরা নতুন কিছু খুঁজছি, নিত্য নতুন পণ্য ও সেবা কিনে চলছি নিরন্তর।
সাত
আমরা এখন বিশ্বায়নের যুগে বাস করছি। তবে এমনটা নয় যে সবাই এতে খুশী। সমালোচনাকারীদের দাবি বিশ্বায়ন সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে ধ্বংস করে পৃথিবীকে একটি সমরূপ (homogenous) সমাজের দিকে এগিয়ে নিচ্ছে। তাদের দাবি যে একেবারে মিথ্যা, তাও নয়। তবে বিশ্বায়নের একটি বড় সুফল রয়েছে। এটি পৃথিবীকে একটি অধিকতর শান্তির গ্রহে পরিণত করছে।
বর্তমানে প্রায় সব দেশ তথা জাতিগোষ্ঠীগুলো নিজেদের উন্নয়নের জন্য একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। বিশ্বায়নের এই পৃথিবীতে প্রতিটি দেশেরই বানিজ্য ও বিনিয়োগের জাল বিস্তৃত থাকে অন্যান্য অনেক দেশের সাথে। ফলে কোন অঞ্চলে বা দেশে যুদ্ধ হলে বিশ্ব অর্থনীতিতে তার প্রভাব পড়ে। আর এজন্যই আমেরিকা, ইউরোপ, এশিয়া তথা সব অঞ্চলের নেতারাই সর্বসম্মিলিতভাবে চেষ্টা করে পৃথিবীকে শান্তি বজায় রাখার। কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে এটি বেশ ভালভাবে কাজ করছে। ১৯৪৫ সালের পর থেকে (একমাত্র ব্যতিক্রম ইরাক কর্তৃক কুয়েত আক্রমণ) কোন স্বাধীন রাষ্ট্রকেই অন্য আরেকটি রাষ্ট্র দ্বারা দখল করতে দেখা যায়নি। একবার চিন্তা করে দেখুন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত পৃথিবী কতটা হিংস্র ছিল, আর বর্তমানে কী অবস্থায় আছে।
মানব জাতি তার ইতিহাসে এতটা শান্তিপূর্ণ সময় আর পার করেনি। এটা খুব আশ্চর্য শোনাতে পারে যে দুটো বিশ্বযুদ্ধে কয়েক কোটি লোক নিহত হওয়ার পরেও বিংশ শতাব্দীই ছিল মানব ইতিহাসের সবচেয়ে শান্তিপূর্ণ শতাব্দী। সত্যিকারার্থে কৃষি বিপ্লবের পর থেকেই মানুষ হিংস্রতা পরিহার করতে শুরু করে এবং ক্রমাগত শান্তির দিকে ধাবিত হয়। এটা অনুমান করা হয় যে কৃষিতে অভ্যস্ত হওয়ার পূর্বে মানুষ যখন শিকারী-সংগ্রাহক অবস্থাতে ছিল তখন সমস্ত বয়স্ক পুরুষের ৩০ শতাংশ গোত্রদন্দ্বে হত্যার শিকার হতো। বর্তমান সময়ে এই পরিসংখ্যান মাত্র এক শতাংশ। এতেই বুঝা যায়, আমরা কতখানি উন্নতি করেছি। কিন্তু কেন এমন হলো?
কৃষি বিপ্লবের ফলশ্রুতিতে যে শ্রেণিবিভাজিত ও কাঠামোভিত্তিক (hierarchical, structured) সমাজ গঠিত হয়েছিল তাতে হত্যা, জবরদস্তি ও অন্যান্য অপরাধের শাস্তির জন্য আইন প্রণীত হয়েছিল। মূলত এর ফলে সমাজে স্থিততা আসতে শুরু করে।
তবে আমরা মানব ইতিহাসে সবচেয়ে শান্তিপূর্ণ সময়ে বাস করছি, এটা ভেবে গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দিলে চলবে না। সম্ভাব্য বিরোধের উৎস সম্পর্কে আমাদেরকে সবসময় সজাগ থাকতে হবে, কেননা আনবিক অস্ত্রসমৃদ্ধ বর্তমান পৃথিবীতে একটা বড় ধরণের আন্তর্জাতিক যুদ্ধ ডেকে আনতে পারে নজিরবিহীন ধ্বংস ও মৃত্যু। হ্যাঁ, আমরা সময়টা উপভোগ করবো, এবং একই সাথে এই শান্তিপূর্ণ অবস্থা টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যে কাজ করতে হবে।
আট
গত তিন লক্ষ বছরে মানুষের ভ্রমণের গল্প শেষ। পূর্ব আফ্রিকার সাভানা থেকে শুরু করে আমরা এসে পৌঁছেছি আধুনিক বিশ্বায়নের পৃথিবীতে। আমরা কিছুটা হলেও ইতিহাসজুড়ে মানুষের সাধারণ প্রবণতাকে বুঝতে পেরেছি। এবার আমরা দেখবো ব্যক্তি মানুষে এই পরিবর্তনে প্রভাব কতটা। যদিও আমাদের স্বাস্থ্য, সম্পদ ও জ্ঞানের প্রভূত উন্নতি হয়েছে, কিন্তু তাতে কি আমরা আগের চেয়ে সুখী হয়েছি?
হতাশাজনকভাবে বলতে হচ্ছে, ব্যক্তি মানুষের ক্ষেত্রে এর উত্তরটি সম্ভবত না বোধক। কৃষিবিপ্লবের সময়ে চাষাবাদ করতে শিখে মানুষের সমষ্টিগতভাবে পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতাও বেড়েছিল। অথচ একজন ব্যক্তিমানুষের জীবন হয়ে গিয়েছিল আরো রুক্ষ। একজন সংগ্রাহকের তুলনায় একজন কৃষককে একদিকে কাজ করতে হতো অনেক বেশি, অন্যদিকে তার খাবারের বেচিত্র্য আর পুষ্টিগুণ ছিল কম। রোগভোগের আশঙ্কাও কৃষকদেরই বেশি ছিল। আবার ইউরোপের দিকে তাকালে দেখা যায়, সাম্রাজ্য বিস্তারের ফলে তাদের সমষ্টিগত ক্ষমতা অনেক বেড়েছে, তাদের আদর্শ, চিন্তাধারা, প্রযুক্তি আর বৈচিত্র্যময় খাবার ছড়িয়ে পড়েছে সারা পৃথিবীতে, বাণিজ্যের নতুন নতুন পথ তেরি হয়েছে। অথচ আফ্রিকা, আমেরিকা আর অস্ট্রেলিয়ার কোটি কোটি আদিবাসী মানুষকে তা অন্তহীন দুর্ভোগ ছাড়া আর কিছুই দেয়নি। মানুষের মধ্যে ক্ষমতা পেলেই সেটা অপব্যবহার করার একটা প্রবণতা আছে। কাজেই ক্ষমতার চর্চার মাধ্যমে মানুষ সুখী হবে, এমনটা ভাবা বোকামি।
মনোবৈজ্ঞানিক গবেষণায় দেখা গেছে সাময়িকভাবে মানুষের সুখ বা দুঃখের বড় রকমের তারতম্য হয় বটে, কিন্তু দীর্ঘ মেয়াদে মানুষের সুখ একটা নির্দিষ্ট মাত্রায়ই অবস্থান করে। উদাহরণস্বরূপ, ধরো তুমি চাকরি হারিয়েছো কিংবা তোমার প্রেমিকা তোমাকে পরিত্যাগ করেছে। তোমার সুখের মাত্রা খুব নিচে নেমে গিয়েছে; তুমি ভাবছো শীঘ্র তোমার এই অবস্থা থেকে উত্তরণ সম্ভব হবে না। কিন্তু দেখা যাবে কিছু দিনের মধ্যেই আরেকটা চাকুরি না পেয়েও কিংবা আরেকজন প্রেমিকা না জুটলেও তোমার সুখের মাত্রা আবার পূর্বের স্বাভাবিক অবস্থানে ফিরে যাবে।
ফরাসি বিপ্লবে সামন্তবাদের অবসান হলে ফ্রান্সের কৃষকরা মুক্তির স্বাদ পায়। স্বভাবতই, তারা উচ্চমাত্রার সুখ অনুভব করে। কিন্তু সেই সুখ কোন স্থায়ী সুখ ছিল না। পরের বছরই হয় তো কোন কৃষক তার অথর্ব সন্তানের ভবিষ্যত আশঙ্কায় দুঃখী হয়েছে, কেউ হয় তো দুঃখী হয়েছে পরের বছরের ফলনের অনিশ্চয়তা আশঙ্কায়।
অনেকের মতে, মানুষের সুখী না হওয়ার কারণ নিহিত রয়েছে আমাদের বিবর্তনে। বিবর্তন মানুষকে দেহে-মনে একটা শিকারি-সংগ্রাহক প্রাণী হিসেবেই তৈরি করেছিল। সেখান থেকে প্রথমে কৃষিনির্ভর ও তার পরে শিল্পনির্ভর জীবনে প্রবেশ করে মানুষ তার প্রাকৃতিক জীবন হারিয়েছে। এই কৃত্রিম জীবন তার চাওয়াগুলো পূরণ করতে পারছে না, তার সহজাত প্রবৃত্তিকে বিকশিত হতে দিচ্ছে না। তাই তার সন্তুষ্টিও হচ্ছে না। আদিম মানুষের ম্যামথ শিকারের যে সুতীব্র উত্তেজনা আর বুনো উল্লাস, তা আজকের একটা শহুরে মধ্যবিত্ত পরিবার কল্পনাও করতে পারবে না। অতএব এটা বলা যুক্তিসংগত যে, আমাদের প্রত্যেকটা নতুন আবিস্কার আমাদেরকে আমাদের কাঙ্ক্ষিত স্বর্গ থেকে একটু একটু করে দূরে নিয়ে যাচ্ছে।
আপাতদৃষ্টিতে দেখলে সম্পদ, সুস্বাস্থ্য এবং সামাজিক বন্ধনকে সুখের নিয়ামক ধরা যায়, তবে বাস্তবতা হলো এর কোনটির বা সবগুলোর ওপরও আসলে সুখ নির্ভর করে না। বরং সেটা নির্ভর করে মানুষের অবস্থা ও তার ব্যক্তিগত চাহিদার ওপর। যদি কেউ একটা গরুর গাড়ি চায়, তাহলে গরুর গাড়ি পেলেই সে সন্তুষ্ট, আর কিছু দরকার নেই। কিন্তু কেউ যদি একটা ঝকঝকে নতুন ফেরারি গাড়ি চায়, একটা পুরোনো ফিয়াট গাড়ি পেয়ে তার মন ভরবে না। যখন আমাদের অবস্থা ভালো থাকে, আমাদের চাহিদাগুলোও ফুলেফেঁপে ওঠে, তাই বড় বড় প্রাপ্তিগুলোও তখন আমাদের সুখ দিতে পারে না। আবার যখন পরিস্থিতি খারাপের দিকে যায়, তখন আশার বেলুনও চুপসে যায়, তাই সেই খারাপ পরিস্থিতিতেও নিজেকে অসুখী মনে হয় না।
অনেকের মতে, মানুষ সম্ভবত এভাবেই তুষ্টি ও হতাশার মধ্যম এক মাত্রায় উত্তরিত (evolved) হয়েছে যাতে না সে অতিরিক্ত মানসিক আঘাতে ভেঙে পড়ে, না আত্মতুষ্টিতে ভুগে বড় ও মহৎ কিছু করার প্রচেষ্টা থেকে নিজেকে বিরত রাখে।
অতএব এটা দেখা গেলো যে, ব্যক্তিক স্তরে মানুষ খুব একটা সুখী নয়। সামাজিক স্তরে তাহলে কী? মানুষের জীবন মানের যেরকম উন্নতি হয়েছে, তাতে নিশ্চয়ই আমরা পূর্বের থেকে অনেক বেশি সুখী।
এটা নির্ভর করছে তুমি কে তার ওপর। অদ্যাবধি মানুষের যে সমৃদ্ধি হয়েছে, তা পকেটগত হয়েছে গুটি কয়েক মানুষের। এর বাইরে যারা আছে, তারা ঐ গুটি কয়েকের থেকে যোজন যোজন দূরে অবস্থান করছে। ঐতিহাসিকভাবে তারা কখনও বা শিকার হয়েছে ঔপনিবেশিকতার, কখনও বা পুঁজিবাদের। খুব অধুনাই তারা আইনী স্বীকৃতি পেয়েছে সমাধিকারের।
নয়
মানুষের ভবিষ্যত কী? আগামী দশকগুলোতে বিজ্ঞানের অগ্রগতি মানুষকে মানে হোমো স্যাপিয়েন্সকে কোথায় নিয়ে পৌঁছাবে?
বিজ্ঞানীরা বর্তমানে বায়োনিক্স এবং বয়স প্রতিরোধ সংক্রান্ত বিষয়ে গবেষণা করছেন। বায়োনিক্সের ক্ষেত্রে মানে যন্ত্র ও মানুষের একত্রীকরণে (merging of human with machine) বিজ্ঞান প্রভূত উন্নতি সাধন করেছে। উদাহরণস্বরূপ, ইলেকট্রিসিয়ান জেসি সুলিভানের কথা বলা যেতে পারে। দুর্ঘটনায় সুলিভান তার দুটি হাতই হারালে বিজ্ঞানীরা তার শরীরে বায়োনিক হাত প্রতিস্থাপিত করেন যেগুলোকে সে তার চিন্তা ও স্নায়ুতন্ত্র দিয়ে পরিচালনা করতে পারে।
বয়স প্রতিরোধেও বিজ্ঞানীদের অগ্রগতি আশানুরূপ। জিন কাঠামোতে পরিবর্তন এনে তারা কৃমি জাতীয় একটি প্রাণীর আয়ু দ্বিগুণ করতে সক্ষম হয়েছেন। ইঁদুরের ক্ষেত্রে প্রয়োগের প্রক্রিয়া চলছে এখন। একদিন যে মানুষের ক্ষেত্রেও এটা সক্ষম হবে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।
বর্তমানে আইনগত ও নৈতিক বাঁধার মুখে মানুষের ক্ষেত্রে এ বিষয়ক গবেষণাকে সীমিত রাখতে হচ্ছে। তাই বলে সে বাঁধা চিরকাল থাকবে, এমনটা মনে করার কোন কারণ নেই। মানুষ যদি কোনদিন চিরকাল বেঁচে থাকার সামান্যতম সুযোগও পায়, তার সামনে থাকা সকল বাঁধাই সে অতিক্রম করবে।
সেদিন খুব বেশি দূরে নয় যেদিন বিজ্ঞালব্ধ জ্ঞানের প্রয়োগে মানুষ প্রজাতিটি তার শরীরের এমন পরিবর্তন করবে যে টেকনিক্যালি তাকে আর হোমো স্যাপিয়েন্স বলা যাবে না। আমরা একটি নতুন প্রজাতিতে পরিণত হব – অর্ধেক জৈবিক আর অর্ধেক যান্ত্রিক। খুব সম্ভাবনা রয়েছে সেই নতুন প্রজাতির প্রতিটি মানুষ হবে কমিক মুভির একেকটি অতিমানব। একমাত্র প্রশ্ন হলো কখন আসবে সেই দিন?
[প্রবন্ধটি লেখা হয়েছিল সাপ্তাহিক অনলাইন পাঠচক্র ‘খাপাছাড়া আড্ডা’য় পাঠ করার উদ্দেশ্য।]